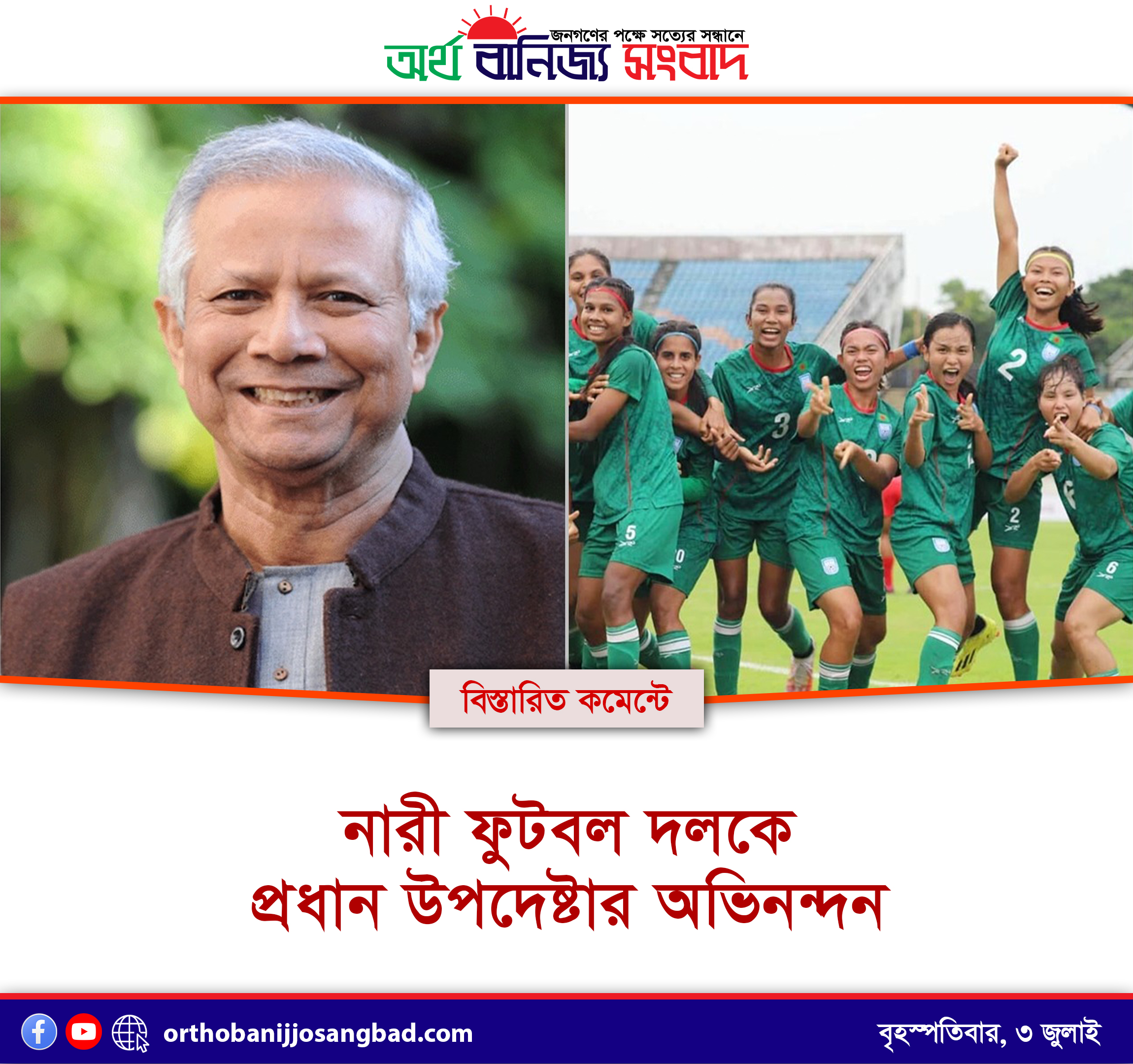মাতৃভাষা বাংলা চর্চা প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা
…..শামসীর হারুনুর রশীদ
ভাষার সংজ্ঞা নিয়ে বিদগ্ধজনের মাঝে বিতর্ক থাকলেও সকল মতের সারাংশ হলো মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের ধ্বনিকে ভাষা বলে। অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠনির্গত সুনির্দিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা। মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন এই ভাষা মানব জাতি কখন, কোথায়, কিভাবে ভাষার ব্যবহার করে প্রথমে? সেই ইতিহাস ভাষা তাত্ত্বিকদের অজানা। ভাষা আবিষ্কারে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য আজো দিতে পারেন নি গবেষকেরা। এক্ষেত্রে যত থিওরি বা তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, এর মোদ্দা কথা হচ্ছে ভাষা আল্লাহ প্রদত্ত, এর সৃষ্টিকারক মহান আল্লাহ। পৃথিবীতে বহুভাষার প্রচলন ও মানব জাতির ভাষার ভিন্নতা আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পবিত্র কুরআনের সুরা রুমের ২২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, ‘‘তার কুদরতের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে- নভোম-ল ও ভূম-লের সৃজন এবং পৃথক পৃথক হওয়া তোমাদের ভাষা।’’ ভাষা যেহেতু মনের ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন এবং জ্ঞান অর্জন বা চর্চারও মাধ্যম, তাই মহান আল্লাহ প্রথম মানব হযরত আদমকে জ্ঞান দান করার আগে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সুরা-রহমানের ৩নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘‘খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান’’ অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ হয়েছে জ্ঞানের মাধ্যমে। আর জ্ঞান অর্জন ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়, তাই ভাষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা বুঝানোর প্রয়োজন আর আছে বলে মনে হয়না।
মাতৃভাষার গুরুত্ব : বিশ্ব জগতে অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে যেমন নানা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, মানবজাতির মধ্যেও তেমনি নানা বর্ণ-গোত্র ও ভাষার মাধ্যমে বৈচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব বৈচিত্রের মাধ্যমে মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বহি:প্রকাশ ঘটেছে। কুরআনের ভাষা হিসেবে আরবি, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রতি যেমন আমরা শ্রদ্ধাশীল, তার চেয়ে হাজার গুণ বাড়িয়ে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা উচিত। সম্ভবত মাতৃভাষার গুরুত্ব বুঝাতে মহান আল্লাহ সুরা ইব্রাহিমের ৪নং আয়াতে নাযিল করে ঘোষণা করেন, ‘‘আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি। তাদের নিকট পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।’’ এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় পৃথিবীতে যুগে যুগে মহান আল্লাহ ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ ২৪ হাজারের মত নবী রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের স্বজাতীয়দের ভাষাভাষী করে। আর প্রত্যেক নবী-রাসুলকে নিজ মাতৃভাষায় ওহীও নাযিল করেছেন। সে বিবেচনায় ধারণা করা যেতে পারে যে, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এবং সব প্রধান ভাষাতেই আল্লাহ তায়ালা ওহী প্রেরণ করেছেন। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও কোন ভাষাকে উপেক্ষ বা অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। কেননা এ আয়াতে মাতৃভাষার গুরুত্ব ও তাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে যথাযথ ভাবে।
ভাষার জন্ম বা উৎপত্তিকাল : এ সম্পর্কে ভাষাতত্ত্ববিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, ‘‘ভাষার জন্ম জীবের জন্মের মতো নয় যে, অমুক সন- তারিখে অমুক ভাষার জন্ম হয়েছে বলা যাবে। বরং ভাষা নদীর প্রবাহের ন্যায়। বিভিন্ন স্থানে তার বিভিন্ন নাম, যখন একটি ভাষা প্রবাহের মধ্যে কোন সময়ের তাহার পরবর্তী ভাষা-ভাষীদিগের নিকট একটি নতুন ভাষা বলিয়া বোধ হয় তখন তার নাম রাখা হয়।’’ (বাংলা সাহিত্যের কথা, রেনেসা প্রিন্টার্স, ঢাকা। এপ্রিল ১৯৫৩ পৃ-১) ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন বলেন, ‘‘ভাষা মানুষের জন্ম সূত্রে পাওয়া, তাহা এতই স্বাভাবিক যে, চলাফেরা বা শাসক্রিয়ার মত স্বয়ংক্রিয় বৃত্তি বলিয়া মনে হয়। মানুষের উচ্চারিত অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।’’ (ভাষার ইতিবৃত্ত-ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা-১৯৭৫)
বাংলা ভাষার জন্ম : বাংলা ভাষার উৎপত্তি কখন, কোথায়, কিভাবে হয়েছিল তার সঠিক হিসাব মিলাতে পারেননি ভাষা গবেষকেরা। এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরণের মত প্রচলিত আছে। বিশ্ব বিখ্যাত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল রেকর্ডে বলা হয়েছে। ‘‘কোন কোন ভাষাবিদ ৫০০ খ্রিস্টাব্দে উড়িয়া ভাষা, বাংলা, অসমীয় এই ৩টি ভাষার জন্ম হয়েছে বলে মনে করলেও বাংলা ভাষাটি তখন পর্যন্ত কোন সুস্থির রূপ ধারণ করেনি। পাশাপাশি সে সময় এর বিভিন্ন লিখিত উপভাষিক রূপ বিদ্যমান ছিল।’’ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত নির্দশন পাওয়া যায় ৬৫০ সাল হতে। অন্যদিকে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তিকাল ৯৫০ সাল হতে। অন্যান্য পন্ডিতগণ এ দুটি মতের সাথে প্রায় সহমত প্রকাশ করেছেন। মূলত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য নামক সন্ন্যাসী কর্তৃক রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’-এর রচনাকাল অনুমান করেই ড. শহীদুল্লাহ ৬৫০ সালেকেই বাংলা সাহিত্যের উজানের সীমা নির্ধারণ করেছেন (আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ পৃ-১৩) কোন ভাষা জন্মের সাথে সাথেই তো আর সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। তবে বাংলা ভাষার উন্মেষ, বিকাশ এবং পরির্বতনের ইতিহাসও খুব একটা সুখের নয়। প-িতগণ আমাদের মাতৃভাষার মূল অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে পূর্ব ইউরোপীয় ও মধ্যে এশিয়ার পশ্চিমে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা-ই ইন্দো-ইউরোপীয় মূলভাষা নামে চিহ্নিত। তার দুটি শাখা ‘কেতুম ও শতম’। শতম শাখার অন্যতম উপশাখা হল ‘আর্য’। এ শাখার আদিম রূপ প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখা নামে পরিচিত। ধারনা করা হয় এর উৎপত্তিকাল ১,৫০০ হতে ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। সংস্কৃত এই সময়ের একটি সাহিত্যিক ভাষা ছিল। তখন জনসাধারণের মাঝে ভাষার যেই আলাদা রূপ প্রচলিত ছিল, তার নাম প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য ভাষা বা আদিম প্রাকৃত ভাষা। এই ভাষা নানা অঞ্চলে বিস্তার লাভ করায় অঞ্চল ভেদে তার রূপভেদও ছিল। পালি এই সময়ের একটি ভাষারূপ। এর পরবর্তী রূপ প্রাচীন প্রাচ্য প্রাকৃত এবং পরবর্তী পর্যায়ে গৌড় প্রাকৃত। গৌড় প্রাকৃতের পরবর্তী স্তর গৌড় অপভ্রংশ। এই গৌড় অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। (আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ পৃ-১৩)
বাংলা ভাষার ইতিহাস ঃ বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত স
বাংলা ভাষার ইতিহাস
বলা ভাষার উৎপত্তিকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে আলোচনার সুবিধার্থে ৫ যুগে বিভক্ত করেছেন বিদগ্ধ জনেরা। ১. প্রাগঐতিহাসিক যুগ: আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগ থেকে খ্রিষ্টীয় সন পর্যন্ত। ২. প্রাক প্রাচীন যুগ: খ্রিষ্টপরবর্তী সময় থেকে নিয়ে ৬৫০ সাল পর্যন্ত। এই যুগদ্বয়ে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন কোন অস্তিত্ব ছিলনা। তখনের ভাষা পরিবার ও তার ধরণ প্রসংঙ্গে বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়ায় বলা হয়, ‘‘বাংলা ভাষাপরিবার ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো ইরানীয়, ইন্দো-আর্য, পূর্ব ইন্দো-আর্য, বাংলা-অসমীয়, বাংলা। প্রারম্ভিক ধরণ মাগধী-পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ-অবহঠঠ-পুরণ বাংলা- বাংলা।’’ ৩. প্রাচীন যুগ: ৬৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলা হয়। এসময়ের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ‘চর্যাপদ।’ কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ, ডোম্বীপাদ, চেন্ডনপাদ, শবরী পাদ ছিলেন এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। ৪. মধ্যযুগ: ১২০১ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগ বলা হয়। বড় চন্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’ মধ্যযুগের অন্যতম সাহিত্য নিদর্শন। এছাড়া মধ্যযুগে আরো অনেক সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। শাহ মুহাম্মদ সগীর, দৌলত কাজী, আলাওল, দ্বিজ চন্ডীদাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, সাবরিদ খান, মুহম্মদ কবীর, দৌলত উজির বাহরাম খান, ভারত চন্দ্র মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য কবি। ৫. আধুনিক যুগ: ১৮০১ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা হয়। বাংলা ভাষায় বিশুদ্ধ গদ্যের প্রচলন আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর মশারফ হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্দীন, ফররুখ আহমদ, হুমায়ুন আহমদ, আল-মাহমুদ, মাওলানা আকরাম খা, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, আহসান হাবীব প্রমুখ আধুনিক যুগের কবি সাহিত্যিক।
প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা ঃ বাংলা ভাষা জন্ম লাভের পর দীর্ঘ ইতিহাস মাড়িয়ে বিভিন্ন স্তরের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে উন্নিত হয়েছে। এই দীর্ঘ কালের যাত্রা পথে, শাসক-শাসনের পরিবর্তনে বাংল ভাষাটি ষড়যন্ত্র ও অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হতে হয়নি যে তা কিন্তু নয়। ইতিহাসে এমনও সময় পার হয়েছে যে, এ ভাষার চর্চাকারীদের রৌরব নামক নরকের ভয় দেখানো হত। কখনো অসুর-যবন-শুদ্রের ভাষা বলে ঘৃণার সাথে উপেক্ষা করা হত। এ ভাষায় কথা বলার অধিকার আদায়ের জন্য রক্তাক্ত আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসও রয়েছে তার। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। নোবেল পুরষ্কার অর্জনের পর বাংলা ভাষার মুকুটে সবচে উজ্জ্বলতম পালকটি যোগ হয় ১৯৯৯ সালে। সে বছরের ১৭ নভেম্বর আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে ইউনেসকো। বাংলা ভাষার ইতিহাসে এ এক গৌরবময় ঘটনা। দেখার বিষয় হল বাংলা কি তার নিজ দেশে প্রাপ্য মর্যাদা পুরোপুরি পাচ্ছে? এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, তাই বলে বাংলার অগ্রযাত্রা থেমে নেই।
বায়ান্ন থেকে ২০১৬ বিগত ৬৪ বছরের বাংলা ভাষার ইতিহাস যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অর্জন সম্ভব হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তার মধ্যে মূলত সাহিত্যই উল্লেখযোগ্য। আমরা অনেক ভাল গল্প, উপন্যাস, কবিতা, অনুবাদ পেয়েছি। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রসারের ক্ষেত্রে যে জায়গাটাতে দুর্বলতা রয়েগেছে তা হল বাংলা এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের র্চ্চার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যেসব মনীষী বিভিন্ন বিষয়ে পারর্দশিতা অর্জন করেছেন. প্রায় সকলেই ইংরেজীতে লেখেন। কারণ হয়ত বা তারা উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব মেনেই। তবে অর্থনৈতিক কারণটাকে বড়ে করে দেখা হয়। এ কারণেই হয়তো জ্ঞান- বিজ্ঞানের উন্নত র্চ্চা করতে হলে যে পরিমাণ বই পুুস্তক থাকা প্রয়োজন, সে পরিমাণ বই বাংলা ভাষায় সৃষ্টি হয়নি। আবার এসব কম বিক্রি হয় বিধায় প্রকাশকরা নিজ উদ্দ্যোগে তা প্রকাশ করতে আগ্রহী নয়। এদিক দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর দিকে থাকলে হতাশার পাল্লাই ভারি মনে হয়। যেমন ডাচ বা ফরাসি ভাষাভাষী জনসংখ্যার তুলনায় তাদের যত বই আছে, আমাদের বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যার তুলনায় তত বই নেই। যতক্ষণ না বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণ মান সম্পন্ন গ্রন্থের সৃষ্টি হচ্ছে, ততক্ষণ বাংলার কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়।
একটি ভাষা যতটুকু বয়স হলে কাঙ্খিত লক্ষে পোছার কথা, বাংলা ভাষা সে বয়স পেয়েছে কিনা কিংবা পেলে তা কবে অতিক্রম করেছে? এ নিয়েও বির্তক চলতে পারে। তবে আনন্দ ও বেদনা নিয়ে বলা যায় যে, বহুকাল হতে বহুতর সামাজিক রাজনৈতিক প্লাবনের মুখোমুখি নানাস্তর পাড়ি দিয়ে বাংলা সাহিত্য উচ্চতা-কঠিনতা এবং নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির পথে যখন অগ্রসরমান, সম্প্রতি সেই পথে পলি পড়ার দৃশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এর কোথাও জলা, কোথাও বালি আবার কোথাও মাটি। সাফ কথা হল- স্বাধীনতা পূর্বাপর ইংরেজি-ফার্সি-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা গেলেও অতি সম্প্রতি হিন্দির প্রভাব লক্ষণীয়। তাছাড়া আমাদের আইনের ক্ষেত্রে বাংলা এখনও নিগৃহীত! উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহৃত হয়না। বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চ শিক্ষায় বাংলার সফল ব্যবহার কেউ করছেনা। খুদ ভাষা দিবসের ব্যানার ফেস্টুন ইংরেজিতে লেখা দেখা যায়। কোথাও হিন্দি গান বাজিয়ে ভাষা দিবস অনুষ্ঠান উদযাপন করতে দেখা যায়। অন্যভাষার প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও নিজ ভাষার ওপর প্রাধান্য দিতে পারিনা।
বাংলা ভাষাকে নিয়ে যাদের ষড়যন্ত্রের শেষ নেই, তাদের সাথে এই ভাষাকে যখন একাকার করা হয়, স্বাধীনতার পরও যারা কলকাতাকে বাংলা সাহিত্যের রাজধানী বলেন কিংবা ভাবেন, হিন্দি ও ইংরেজি প্রেমিক লেখক- সাহিত্যিককে বাংলা ভাষার মুরব্বি সাব্যস্ত করেন বা অগ্রাধিকার দেন, তাদের মুর্খতা দেখে আমাদের করুণা হয়। আমরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হই। বলা বাহুল্য বলা বাহুল্য, হিন্দি-সংস্কৃতি-ইংরেজি-উর্দুর ছায়া তলে বসে যারা বাংলা চর্চা করেছেন বা করছেন তাদের সাধুবাদ ও উৎসাহ দিতে আমাদের কোন কার্পণ্যতা নেই। কিন্তু সাহিত্যের দিক নির্দেশক আমরা মানতে পারিনা। হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা কলকাতা ওয়ালাদের গ্রাস করে নিচ্ছে খুব সহজে। সেখানের বাঙালীরা বাংলা ভাষা রক্ষার জন্য যেভাবে চেষ্টা করার ছিল, সেভাবে করছেন বলে মনে হয়না।
সুতরাং বাংলার প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়াতে প্রয়োজন বুদ্ধি বৃত্তিক দাসত্বের উর্দ্ধে উঠে জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি মূল ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা।
ভিন দেশে বাংলা চর্চা ঃ ১৪ জুলাই ২০১১, দক্ষিণ সুদান স্বাধীন হওয়ার পর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীর ১৯৩ টি দেশের ৭১০ কোটি মানুষ ‘‘২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’’ সম্পর্কে জানে। ৭১০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ২৮ কোটি লোক বাংলা ভাষী। জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে যার অবস্থান সপ্তম, আর মাতৃভাষার দিক থেকে পঞ্চম (৬ষ্ঠ?)। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১১ সালে প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ছোট বড় মিলে পৃথিবীতে ৭২১১ টি ভাষার অস্তিত্ব রয়েছে। তার মধ্যে একমাত্র বাংলা ভাষা, যে ভাষার জন্য বীর বাঙালী অকাতরে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করেছে। চলমান নিবন্ধে প্রবাসী বাঙালীর চেয়ে বিদেশের যেসব প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে দেশে বর্তমানে বাংলা ভাষা চর্চা চলছে, সে বিষয়ে- বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক-মাসিক পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী তার একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি- মার্কিন গবেষক ক্লিনটন বিসিলির কথা এর আগে আমরা জেনেছি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপক বাংলা ভাষাকেই করেছেন তার ধ্যান জ্ঞান, অনুবাদ করেছেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত ও জীবনান্দ দাশের কবিতা। ইতালির ফাদার মারিনো রিগন বাংলাকে ভালো বেসে থেকে গেছেন বাংলাদেশই। বর্হিবিশ্বে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপূর্বকালে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান আর রাশিয়া আশির দশক পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল, তখন বাংলা ভাষার সেরা ক্লাসিক গ্রন্থ প্রকাশিত হত সেখানে থেকে। ইংল্যান্ডের অনেক সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে বাংলা শেখার ও চর্চার সুযোগ রয়েছে।
তেমনি বাংলা গবেষণা সহ নানা ধরনের প্রকাশনা ও লক্ষ্য করার মত। স্বাধীনতাপূর্ব থেকেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সোয়াসে প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাচর্চা বিভাগের অধীনে বাংলা চর্চা চলছে, চলছে গবেষণাও। এখানে বাংলা ভাষাভাষীদের পাশা-পাশি কাজ করছেন জেডি এন্ডারসন টি ডব্লিউ ক্লার্ক (কেমব্রিজ), জন বোল্টন, উইলিয়াম রাদিচে, হানা টমসন বাংলা বিভাগটি পরিচালনা করছেন সোয়াসে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অদিতি লাহিড়ি বাংলা রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছেন প্রায় দশক ধরে।
দৈনিক প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘‘বাংলা চর্চা এবং গবেষণার অন্যতম দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে কমপক্ষে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও এশীয় গবেষণা কেন্দ্রে বাংলা ভাষা চর্চা হচ্ছে। এর মধ্যে নিউইয়র্ক, ইথাকা, শিকাগো, মিনেসোটা, ফ্লোরিডা, মেরিল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, ভার্জিনিয়া, উইসকনসিন, হার্ভার্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অর্থ প্রকাশে মনস্তত্তের ভূমিকা নিয়ে কাজ করছেন জাস্টিন আলফানসো চাকোন, বাংলাদেশি বংশোদ্ভুব রাশাদ আহমেদ করছেন ওয়াশিংটনে বাংলা স্ল্যাং নিয়ে। নিউইয়র্কে মারিয়া হেলেন বেবো কাজ করেন নজরুল সাহিত্য নিয়ে। তার এ বিষয়ে গ্রন্থও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সলিম উদ-দৌলা খান ও ভারতের ইন্দ্রনীল দত্ত উচ্চতর গবেষণা করছেন বাংলা ধ্বনি বিজ্ঞান নিয়ে। এছাড়া আমেরিকার নিউইয়ের্কের জ্যাকসন হাইটস কিংবা লস অ্যাঞ্জেলেসে গড়ে উঠেছে বাঙালি পাড়া, সেখানে বাংলা ভাষার এক নতুন প্রবাসী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কানাডার জোসেফ ও কনেল, ভ্যাঙ্কুভারে ব্যারি মরিসন প্রমুখ প্রবাসী ব্যক্তি বাংলায় অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিয়োজিত। অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন প্রবাসী বাঙালিদের এক জনগোষ্ঠী, যারা নিয়মিত বাংলা চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেদেশের বিদ্যালয়ে যেসব এশীয় ভাষা শেখার অনুমতি ও গুরুত্ব দিয়েছে, তার মধ্যে বাংলার অবস্থান তৃতীয়। এশিয়ার মধ্যে জাপান, চীন, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বাংলা গবেষণা ও চর্চা রয়েছে। কিয়োতো এবং ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন তরুণ গবেষক হুজিয়ারা। বেডিও এনএইচকেতে বাংলা ভাষা শিক্ষাসহ নিয়মিত বাংলা অনুষ্ঠান হচ্ছে। বেইজিংয়ে বাংলার সম্প্রসার চলে আসছে সেই দীর্ঘদিন থেকে। চীন থেকে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু অনুবাদ কর্মও। ফ্রান্সে ফ্রাস ভট্টাচার্য, মাদান আনসারি, জার্মানে জোসেফ বায়ার, ইতালিতে অধ্যাপক মারামারা, বেলজিয়ামে ফাদার পল দ্যতিয়েন। নরওয়ে থ্রমসো বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যাপক জিলিয়ান রামচান্দ, নেদারল্যন্ডে গবেষক ভিক্টর ভ্যান বিজার্ট, বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করছেন, সম্প্রতি জানা গেছে ডেনমার্কের অলবো বিশ্ব বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি বেঙ্গল স্ট্যাডি সেন্টার খোলা হয়েছে। এছাড়াও দেশে দেশে বাংলা ভাষার ওপর সেমিনার, গবেষণা, কনফারেন্স নিয়মিত হচ্ছে। যা নিশ্চয় আনন্দের বিষয়।
লেখক : মুহাদ্দিস, গবেষক ওপ্রাবন্ধিক