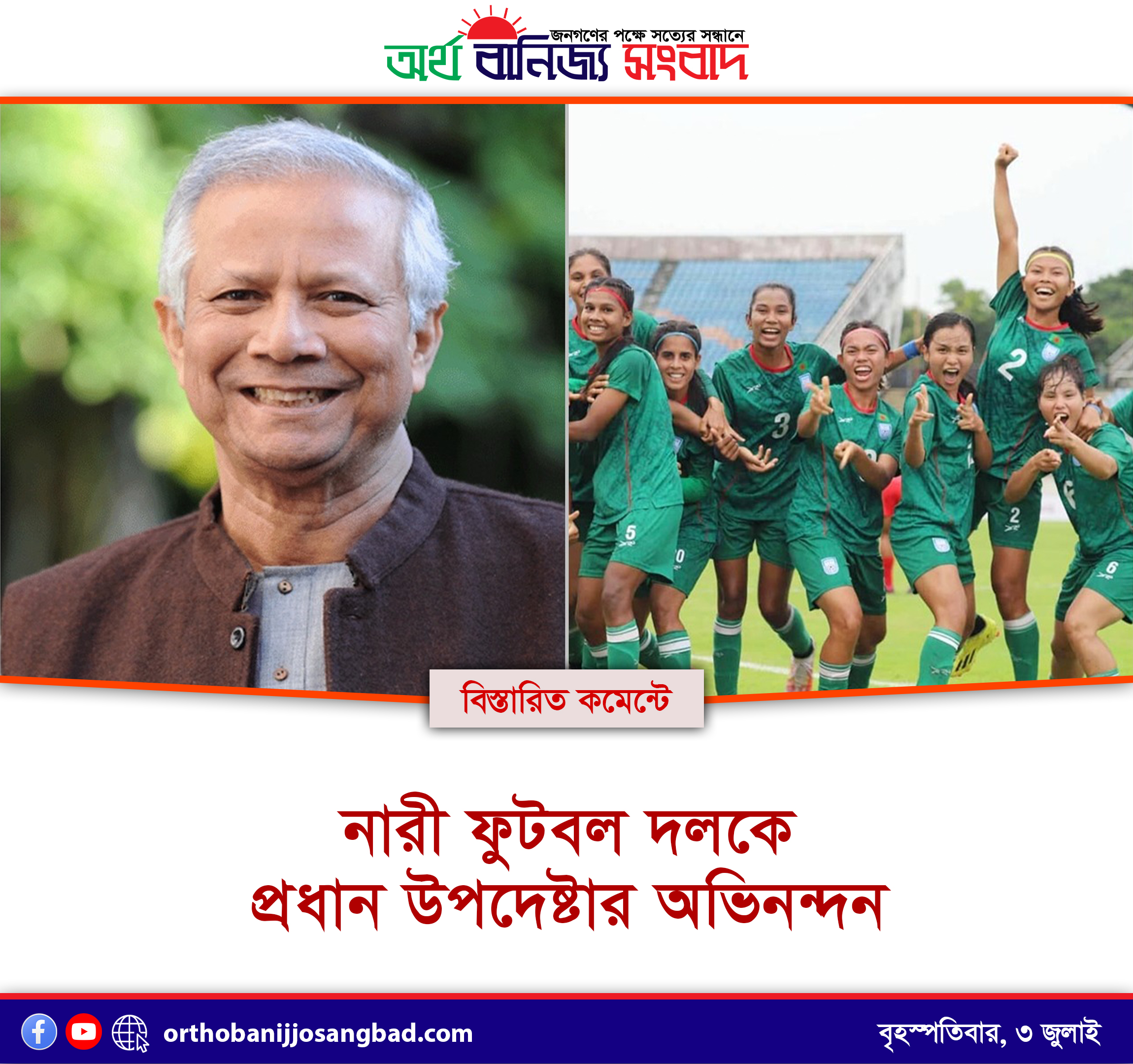রাষ্ট্রভাষা বাংলা : ভাবনার একবিন্দু
…….শামসীর হারুনুর রশীদ
সময় চলে যায় অবিরাম। দিনের পর মাস। মাসের পর বছর। এমনি করে সময় মিশে যায় অন্তকালের মধ্যে। কিন্তু জীবনে এমন দু’একটি দিন আসে যা নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। এমনি স্মৃতি বিজড়িত একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি । এই একুশে রয়েছে, অধিকার আদায়ের গান। রয়েছে সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত সহ জানা অজানা ভাই হারানো ব্যাথা আর বাঙ্গালী হিসেবে জেগে উঠার প্রতিচ্ছবি। তাই বছর ঘুরে বাঙ্গালীদের কাছে শ্রদ্ধার বাণী নিয়ে হাজির হয় এই একুশ। এ দিনটি শ্রদ্ধা গর্ব ও অহংকারের। মাতৃভাষার জন্য জীবন বিসর্জন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।
সেই ইতিহাসের মোড়ক উন্মোচন করে, বাঙ্গালী বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মাতৃভাষার মর্যাদা। পেয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সে দিন সেই রক্তাক্ত রাজপথ দেখিনি, লোক মুখে শুনেছি, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। জানতে পেরেছি পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা ৩০ কোটির ওপরে। তন্মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি মুসলমান। ভাষা গবেষক অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম লিখেন- মূলত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকশিতই হতোনা যদি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে মুসলিম আগমন না ঘটত।
ডক্টর শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেনের ভাষায় ‘‘মুসলমান আগমনের পূর্বে বঙ্গ ভাষা কোন কৃষক রমনীর ন্যায় দীনহীন বেশে পল্লী কুঠিরে বাস করেতেছিল।’’ ইতরের ভাষা বলিয়া বঙ্গভাষাকে পন্ডিত মন্ডলী দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন, হাড়ি-ডোমের স্পর্শ হইতে ব্রাহ্মণেরা যেরূপ দূরে থাকেন বঙ্গভাষা তেমনই সুধী সমাজের কাছে অপাঙক্তেয় ছিল। তেমনি ঘৃনা, অনাদর ও উপেক্ষার পাত্র ছিল। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যকে এক রূপ মুসলমানদের সৃষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি হইবেনা। (দ্র: শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন- বঙ্গভাষার উপর মুসলমানদের প্রভাব)
অধ্যাপক হাসান আব্দুল কাইয়ুম আরো লিখেন, চিত্তাকর্ষক মনোরঞ্জক সাবলীল শব্দ যোজনা ও বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে কোন বিষয়কে ফুটিয়ে তুলে এমন রচনা বা গ্রন্থনাই সাহিত্য। মনের ভাব ও ভাষাকে সাহিত্য ধরে রাখে। সাহিত্যের নানামাত্রিক রূপ ও রস যেমন রয়েছে, তেমনি ধরনগত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা রয়েছে। রয়েছে পদ্য ও গদ্য। রয়েছে ছন্দ মাধুর্য ও ছান্দস সৌকুমার্য। প্রাচীন বাংলার স্বরূপ উদ্ধার ‘চর্যাপদ’কে বলা হলেও তা বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যেই অত্যন্ত সীমিত আকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচরণকৃত এক ধরণের কাব্য-কর্ম যা রাজ রাজাদের চোখ রাঙানো ভয়ে বিস্তৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া এটা বৌদ্ধ সাধনার মধ্যেই সীমিত ছিল আর তাকে বাংলাভাষা বলা দূরূহ। সর্ববোধগম্য বাংলার উন্মেষ তখনই ঘটলো যখন এই ভাষায় আরবী ফারসী শব্দ ক্রমান্বয়ে সংযোজিত হতে লাগলো। পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় আরবী শব্দ দুই হাজার ও ফারসী শব্দ আড়াই হাজারের ও বেশী সংযোজিত হয়েছে। তাছাড়া আরবী ফারসী মিলিত শব্দ ও তুর্কি শব্দ ও রয়েছে অনেক………।
বাংলা ভাষাতে অসংখ্য আরবী শব্দ রয়েছে সেটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য যে, বঙ্গ শব্দের সংগে আরবী ‘আল’ শব্দ যুক্ত করে বঙ্গ আল বা বঙ্গাল, পরে বাঙ্গালা যা বাংলা হয়ে যায় ‘‘সিলেট’’ শব্দের মত।
উৎপত্তি ও বিকাশের দিক থেকে ভাষা গবেষকরা বাংলা ভাষার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন-
১. প্রাচীন যুগ। ২. মধ্যযুগ ৩. আধুনিক যুগ।
প্রাচীন যুগ: এ যুগ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝাঝী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শতাব্দীর যুগ। তখন বাংলায় বৌদ্ধ শাসন ছিল। এ যুগ দু’পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব ৬০০-১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, নিছক বৌদ্ধযুগ।
দ্বিতীয় পর্ব ১০০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু যুগ। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী (৯৫০-১০৫০) এর মাঝামাঝী সময়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বৌদ্ধ কর্তৃক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত ‘‘চর্যাপদ’’ এ যুগের একক সাহিত্য কর্ম।
মধ্যযুগ: এ যুগ (১২০৫-১৮০০) ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয় শতাব্দীর যুগ। ভিন্ন ভাবে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা বিজয় থেকে ইংরেজ কর্তৃক ‘‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’’ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত। এ সময়েই প্রকৃত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টি হয়। এযুগ কে মুসলমানী যুগ বলা হয়। মুসলিম শাসক হোসেন শাহ’র পৃষ্ঠপোষকতায় চন্ডীদাস কর্তৃক লিখিত ‘‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন’’ এ যুগেরই রচনা। এটি প্রথম গ্রন্থ যা খাটী বাংলা ভাষায় লিখা। কৃত্তিবাস কর্তৃক রচিত ‘‘রামায়ন’’ ও মুসলিম শাষক সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ’র তত্তাবধানে হয়েছে। কারণ বাংলার ব্রাহ্মণদের কাছে সংস্কৃত ছিল ‘‘দেব ভাষা’’। বাংলা সহ অন্যান্য ভাষা ছিল শুদ্রের (নীচ) ভাষা, তাদের নিকট ‘সংস্কৃত’ ছাড়া অন্য ভাষায় ধর্মীয় বই লেখা হারাম ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণরা এই বলে বাংলা সাহিত্যকে অভিশপ্ত করেছিল যে, ‘‘যারা অষ্টাদশ, পুরান ও রামায়ন বাংলায় শুনে, তারা রৌরব নামক নরকে যাবে।’’ তাই দশম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুদের রাজত্বকালে বাংলা ভাষার কোন সাহিত্য কর্ম রচিত হয়নি (দ্র: মধ্য যুগের মুসলিম শাসকরাই বাংলা সাহিত্যের স্থপতি- কাজী জাফরুল ইসলাম)
পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার ব্যাপক জোয়ার আসে। মুসলিম লেখকগণ শুরু থেকেই বাংলা চর্চায় আত্ম নিয়োগ করেন। সুলতান ইউসুফ শাহ’র দরবার কবি জৈনুদ্দীন ‘‘রসুল বিজয়’’ কাব্য রচনা করে বাংলায় রাসুল সা.’র পবিত্র জীবনীগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ঘটান। এরপর গীতি কবিতা, পদ্যা পতি, লাইলি-মজনু, মঙ্গল কাব্য, পুতি সাহিত্যসহ ক্রমান্নয়ে বহু ভাষার শব্দ ভান্ডারে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু তখন ও গদ্য চর্চা শুরু হয়নি।
আধুনিক যুগ: উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী। এ যুগ বাংলা সাহিত্যের সংগঠন ও বিস্তার যুগ। এ যুগের সুচনালগ্নে রাজনৈতিক ও সাহিত্যাঙ্গনে বহুমুখী বিপর্যয় দেখা দেয়।
এক. ১৭৫৭ সালে ইংরেজ কর্তৃক নবাব সিরাজুদ্দৌলার নির্মম পতন ও ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন।
দুই. ১৮০১ সালে কলকাতায় ‘ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ’’ প্রতিষ্ঠা; যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য থেকে আরবী-ফার্সী শব্দ বাদ দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইসলামী প্রভাবমুক্ত করা।তিন. ১৮৩৫ সালে রাষ্ট্রভাষা ফার্সীকে হঠিয়ে ইংরেজীকে দেয়া হয় রাষ্ট্রভাষার মান। এসব পট পরিবর্তনের আড়ালে ছিল বাঙ্গালী মুসলমানকে পেছনে ফেলার সুগভীর ষড়যন্ত্র। আত্মঅভিমানী কিংকর্তব্য বিমূঢ় বাঙ্গালি মুসলমান অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করতে পারেনি। যখন তারা প্রবেশ করেছে তখন অন্যরা বহু দুর অগ্রসর হয়ে পড়ে। মীর মোশাররফ হুসেনের ‘‘বিষাদ সিন্ধু’’ ও কায়কোবাদের ‘‘অশ্রুমালা’’ এসময়ের অনবদ্য রচনা।
আসাদ বিন হাফিজ লিখেন: মুসলমানদের বিপর্যয়ের সুযোগে হিন্দু কবি সাহিত্যিকগণ ভাষার রূপ এতটাই পাল্টে দিতে সক্ষম হন যে, একদিন যে ভাষাকে তারা কাক-পক্ষীর ভাষা বলতেন, যে ভাষার শাস্ত্র চর্চা করলে রৌরব নরকের ভয় দেখাতেন, সে ভাষাকেই তারা সংস্কৃতির দুহিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে বসলেন (দ্র: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস- সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়)
আধুনিক যুগে হিন্দু পন্ডিতদের ব্যাপক ভাবে বাংলা ভাষা চর্চার ভূমিকা দেখে আমাদের কথিত বুদ্ধিজীবীরা এমন সাহিত্য ভাষায় অবতরণ করছেন যে, ‘‘মামদু ভুত ও উর্জবুক’র মত নতুন নতুন অনেক শব্দ তারা আমদানি করেছেন। এ শব্দ গুলো ব্যবহার করা যে শিরক, তাও আমরা জানিনা। এগুলো আমাদের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বিরোধী। অনেকের ধারণা হিন্দুরা এখন আর বাংলা ভাষার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে সক্রিয় নেই। কিন্তু এ ধারণাটি ভেঙ্গে দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যে ভাষাকে অবলম্বন করে তিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন, সে ভাষার প্রতি একটা মমত্ববোধ সঙ্গত ভাবেই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের পূর্বে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার দাবি উত্থাপিত হয় ১৯১৮ সালে। তখন রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়ার সর্বাধিক বিরোধীতা রবীন্দ্রনাথই করলেন। হ্যায়! —– মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর এক প্রশ্নের জবাবে কবি রবী ঠাকুর লিখলেন- ভারত বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একমাত্র হিন্দিকেই রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব। তখন রবীন্দ্রনাথের হিন্দি সম্পর্কিত প্রস্তাবের ঘোর বিরোধীতা করেন ড. মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ। ১৯১৮ সালেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায়, সারা ভারত থেকে আগত ভাষাতত্ত¡বিদদের সামনে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করে মনীষা ড. মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ বলেছিলেন, শুধু ভারত কেন সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই বাংলার স্থান হবে সর্বোচ্চ। (দ্র: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়/ বাংলা সাহিত্যের ধারা- মুহাম্মদ শহীদ উল্লাহ/ ভাষা আন্দোলনের ডায়রী মোস্তফা কামাল-১২)
১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর করাচিতে এক শিক্ষা সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ দিকে পূর্ব বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক ছিল বাঙ্গালী। তারা চায় রাষ্ট্রভাষা হোক বাংলা। তখন সর্বপ্রথম ৪৭ সালে একটি ইসলামী আদর্শবাদী সংগঠন ‘‘তমদ্দুন মজলিস’’ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতারা আন্দোলন শুরু করেন। হযরত মাওলানা আতহার আলী রহ. মানুষের নিকট তা গ্রহনীয় করে তুলার জন্য জমিয়তের পাকিস্তানের সংবিধানের এক ধারায় লিখলেন ‘উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। (দ্র: মাসিক মদীনা-ডিসেম্বর-২০০৮/ বদরুদ্দীন ওমর ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি পৃ: ২৪১)
১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে আবারো ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম ভাষা আন্দোলনের প্রতিবাদ দিবস করা হয়। এদিন ঢাকার রাজপথে সাধারণ ধর্মঘট পুরোপরি পালিত হয়।
১৯৪৯ সাল থেকে বাঙ্গালীরা মায়ের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার স্বপ্নে সবুজ রং মেখে নেমে যায় আন্দোলনে। কিন্তু গ্রেফতার, অত্যাচারে দিন গুলো হয়ে উঠল বেদনায় নীল।
১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বরে লিয়াকত আলি খান আবারো গণ পরিষদে ঘোষণা করেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা। তাতে পুর্বাঞ্চলীয়রা আবারো ফেটে পড়ে। তারপর নির্যাতন আর নিপীড়নের মধ্য দিয়ে আসে ২০ ফেব্র“য়ারি ১৯৫২ সাল।
১৯৫২ সালের ২ শে ফেব্র“য়ারি ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। সেদিন পাকিস্তানিরা চিনতে পেরেছিল, বাঙ্গালীরা কারা। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বাঙ্গালী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে। অত:পর জানা-অজানা অনেক আদরের দুলালদের রক্তে রঞ্জিত হল ঢাকার পিচঢালা রাজপথ। মুলত সে কারণেই ২১ ফেব্র“য়ারি জাতিসংঘেও স্বীকৃতি অর্জন করেছে।
অবশেষে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্র“য়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। ফলে বিশ্বের সকল দেশেই প্রতিবছর ২১শে ফেব্র“য়ারি পালিত হয় বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে।
লেখক : মুহাদ্দিস, গবেষক ও প্রাবন্ধিক
০১৭২৬-৮৫৬৬৬৯
E-mail: shamsherharunrashid@yahoo.com